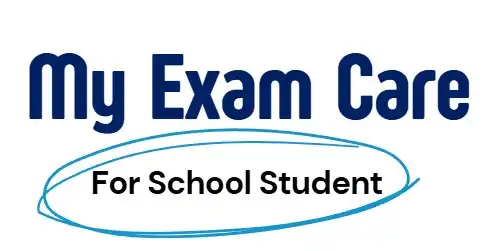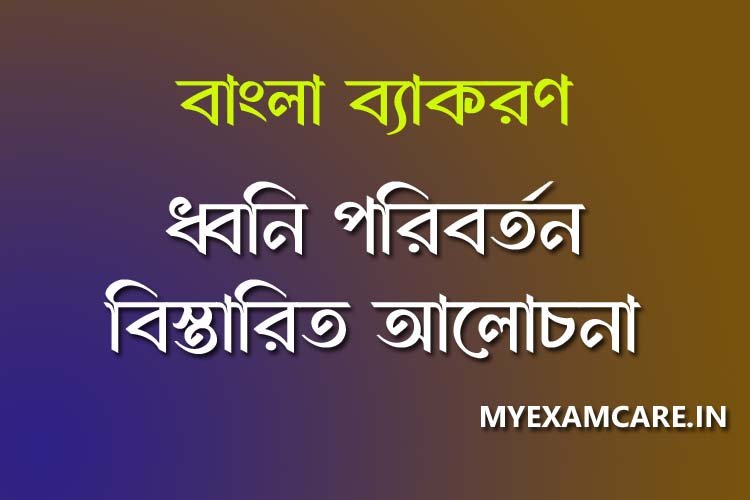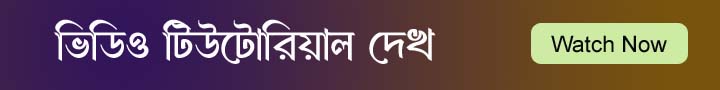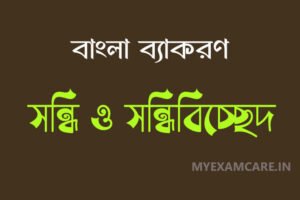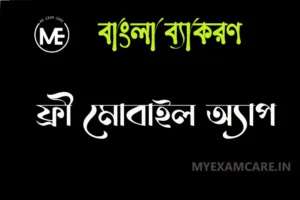বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় একটি অন্যতম বিষয় হল ধ্বনি পরিবর্তন। কী এই ধ্বনি পরিবর্তন ? তা কত প্রকার ? এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়েছে আমাদের আজকের পোস্টে। ছাত্রছাত্রীরা এই আলোচনাটি মন দিয়ে পড়লে আশা করি তোমাদের অনেক সংশয় দূর হয়ে যাবে। তাহলে চল, শুরু করা যাক।
ধ্বনি পরিবর্তন কী ?
উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন কোনো শব্দে ধ্বনিগত বদল আসে এবং তাঁর ফলে শব্দটির যে পরিবর্তন ঘটে তাকেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে। এই ধ্বনির পরিবর্তন স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। ধ্বনির পরিবর্তনের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতির নাম হল – স্বরভক্তি, স্বরসঙ্গতি, সমীভবন, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, বিপর্যাস ইত্যাদি। আমরা একনজরে বিভিন্ন শ্রেণির ধ্বনি পরিবর্তনের রীতিগুলি দেখে নেব।
ধ্বন্যাগম
‘ধ্বন্যাগম’ শব্দের অর্থ ধ্বনির আগমন। যখন কোনো শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্তে কোনো ধ্বনির আগমন ঘটে তখন তাকে ধ্বন্যাগম বলে। ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতি স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। যখন কোনো শব্দে স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে স্বরাগম বলে। আর যখন কোনো শব্দে ব্যঞ্জনের আগমন হয় তখন তাকে ব্যঞ্জনাগম বলে।
ক. স্বরাগমঃ যখন কোনো শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্তে কোনো স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম যেহেতু শব্দের তিনটি অবস্থানেই হয় তাই এই রীতিটি তিনভাগে বিভক্ত – আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম ও অন্ত্য স্বরাগম।
শব্দের আদিতে কোনো স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন – স্কুল > ইস্কুল। এই উদাহরণে মূল শব্দ ‘স্কুল’ -এর আদিতে একটি স্বরধ্বনি ‘ই’ এসেছে এবং শব্দটির পরিবর্তন ঘটে ‘ইস্কুল’ হয়েছে।
মক টেস্ট দিতে ক্লিক কর।
একই ভাবে যখন কোনো শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন তা মধ্য স্বরাগম হয়। যেমন – বয়ন > বয়ান। এই উদাহরণে মূল শব্দ ‘বয়ন’ -এর মধ্যবর্তী ধ্বনি ‘য়’ -এর সঙ্গে ‘আ’ স্বরধ্বনি যুক্ত হয়েছে। শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে ‘বয়ান’ হয়েছে।
শুধু শব্দের আদি বা মধ্যবর্তী অবস্থানেই নয়, শব্দের অন্ত্যেও স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। এমনটি ঘটলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন – সত্য > সত্যি। মূল শব্দ ‘সত্য’ -এর শেষে ‘ই’ স্বরধ্বনির আগমন ঘটে শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে।
খ. ব্যঞ্জনাগমঃ
যখন কোনো শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্তে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে তখন তাকে ব্যঞ্জনাগম বলে। ব্যঞ্জনাগম যেহেতু শব্দের তিনটি অবস্থানেই হয় তাই এই রীতিটি তিনভাগে বিভক্ত – আদি ব্যঞ্জনাগম, মধ্য ব্যঞ্জনাগম ও অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম।
যখন শব্দের আদিতে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে। যেমন – ওঝা > রোজা। এই উদাহরণে মূল শব্দ ‘ওঝা’র আদি অবস্থানে ব্যঞ্জনধ্বনি ‘র’ -এর আগমন হয়েছে।
অনেক ক্ষেত্রে কোনো শব্দের মধ্যবর্তী অবস্থানে কোনো ব্যঞ্জনের আগমন ঘটে থাকে, তখন তাকে মধ্য ব্যঞ্জনাগম বলা হয়। যেমন – বানর > বান্দর। ‘বানর’ শব্দের মধ্যবর্তী ‘ন্’ ব্যঞ্জনের সঙ্গে ‘দ্’ ব্যঞ্জন যুক্ত হয়েছে। ফলে শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে।
কোনো শব্দের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে তখন তাকে অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম বলা হয়। যেমন – নানা > নানান। এই উদাহরণে মূল শব্দ ‘নানা’র অন্ত্যে একটি ব্যঞ্জন ‘ন্’ -এর আগমন ঘটেছে।
স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ
‘স্বরভক্তি’ শব্দটির অর্থ হল ‘স্বরের বিভাজন’। ‘বিপ্রকর্ষ’ শব্দের অর্থ হল ‘ব্যবধান’।
উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে থাকা কোনো সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মাঝে স্বরধ্বনি আনা হলে শব্দটির ধ্বনিগত যে পরিবর্তন হয় তাকেই স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। মনে রাখতে হবে, কবিতায় ছন্দের মাধূর্য সৃষ্টি করতে স্বরভক্তি খুবই সহায়ক।
যেমন – শক্তি (শ্ + অ + ক্ + ত্ + ই) > শকতি (শ্ + অ + ক্ + অ + ত্ + ই) এই উদাহরণে ‘শক্তি’ শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন ‘ক্ত’ -এর মাঝে স্বরধ্বনি ‘অ’ এসেছে। বলা যায় এই ‘অ’ দুটি ব্যঞ্জনের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে। স্বরভক্তির আরও উদাহরণ – ধর্ম > ধরম, ভক্তি > ভকতি, প্রকাশ > পরকাশ, শ্লোক > শোলোক ইত্যাদি।
স্বরসঙ্গতি
শব্দস্থিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে অথবা পারস্পরিক প্রভাবে ঐ শব্দের মধ্যে থাকা অন্য কোনো স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে প্রভাবকারী স্বরের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়।
স্বরসঙ্গতি তিন ধরনের হয় – প্রগত স্বরসঙ্গতি, পরাগত স্বরসঙ্গতি ও অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি। এছাড়া আছে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি।
যখন পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি ঘটে তখন তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন – মিঠা > মিঠে, হিসাব > হিসেব, শিক্ষা > শিক্ষে ইত্যাদি।
পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি ঘটে তবে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলা হয়। যেমন – দেশি > দিশি, ঝুলা > ঝোলা, বিড়াল > বেড়াল ইত্যাদি।
শুধু পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে অপর স্বরের সঙ্গতিই নয়, একটি স্বর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই স্বর আবার অন্য একটি স্বরকে প্রভাবিত করলে অর্থাৎ পারস্পরিক প্রভাবে স্বরের সঙ্গতিও ঘটে। এই রীতিটি অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি নামে পরিচিত। যেমন – পোষ্য > পুষ্যি, ধোঁকা > ধুঁকো ।
আর যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বরের প্রভাবে মধ্যের স্বরটি সঙ্গতি রক্ষা করে তখন তা মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন – ভিখারি > ভিখিরি, জিলাপি > জিলিপি। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, মধ্যগত স্বরসঙ্গতি আসলে প্রগত ও পরাগত স্বরসঙ্গতির মিশ্র একটি প্রক্রিয়া।
ধ্বনিলোপ
কোনো শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্তে যখন কোনো ধ্বনির লোপ ঘটে তখন তাকে ধ্বনিলোপ বলে। ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতি স্বর ও ব্যঞ্জন উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। যখন কোনো শব্দে স্বরধ্বনির লোপ হয় তখন তাকে স্বরলোপ বলে। আর যখন কোনো শব্দে ব্যঞ্জনের লোপ হয় তখন তাকে ব্যঞ্জনলোপ বলে।
ক. স্বরলোপঃ যখন কোনো শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্ত্যে কোনো স্বরধ্বনির লোপ হলে শব্দটিতে ধ্বনিগত যে পরিবর্তন হয় তাকেই স্বরলোপ বলে।
স্বরলোপ তিন ধরনের হয় – আদি স্বরলোপ, মধ্য স্বরলোপ ও অন্ত্য স্বরলোপ।
বলা যায়, শব্দের আদিতে থাকা কোনো স্বরধ্বনি লোপ পায় তখন তাকে আদি স্বরলোপ বলে। যেমন – আনোনা > নোনা, আছিল > ছিল ইত্যাদি।
যদি শব্দের মধ্যস্থিত কোনো স্বরধ্বনির লোপ হয় তবে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন – জানালা > জানলা, কলিকাতা > কলকাতা ইত্যাদি।
আর শব্দের অন্ত্যে থাকা কোনো স্বরধ্বনির লোপ ঘটলে তাকে অন্ত্য স্বরলোপ বলে। যেমন – আজি > আজ, পাতি > পাত ইত্যাদি।
খ. ব্যঞ্জনলোপঃ কোনো শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা অন্ত্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হলে শব্দটিতে ধ্বনিগত যে পরিবর্তন হয় তাকেই ব্যঞ্জনলোপ বলে। ব্যঞ্জনলোপ তিন ধরনের হয় – আদি ব্যঞ্জনলোপ, মধ্য ব্যঞ্জনলোপ ও অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ।
যখন শব্দের আদিতে থাকা কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় তখন তাকে আদি ব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন – স্ফটিক > ফটিক।
যদি শব্দের মধ্যস্থিত কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হয় তবে তাকে মধ্য ব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন – ফাল্গুন > ফাগুন, কার্পাস > কাপাস ইত্যাদি।
আর শব্দের অন্ত্যে থাকা কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ঘটলে তাকে অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন – আলোক > আলো, কুটুম্ব > কুটুম ইত্যাদি।
এছাড়া আছে সমাক্ষর লোপ। এটি এক প্রকারের ব্যঞ্জনলোপ। শব্দের মধ্যে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি সমব্যঞ্জনের একটি লোপ পেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন – পাদোদক > পাদোক, বড়দাদা > বড়দা ইত্যাদি।
ধ্বনি বিপর্যয়
উচ্চারণের সময় শব্দের মধ্যে থাকা দুটি ধ্বনির পারস্পরিক স্থান বিনিময়কে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। এই রীতিটির অন্য নাম বিপর্যাস। যেমন – পিশাচ > পিচাশ। এই উদাহরণে ‘শ্’ এবং ‘চ্’ ধ্বনিদুটি পরস্পরে স্থান বিনিময় করেছে এবং শব্দটিতে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটেছে। এরকম – তলোয়ার > তরোয়াল, আলনা > আনলা, বাক্স > বাস্ক ইত্যাদি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ।
অপিনিহিতি
‘অপিনিহিতি’ শব্দটির অর্থ পূর্বে স্থাপন। যখন কোনো শব্দের মধ্যে যুক্ত থাকা ‘ই’ বা ‘উ’ নিজস্থানে উচ্চারিত না হয়ে যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত তার ঠিক পূর্বে উচ্চারিত হয় এবং তার ফলে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তাকেই অপিনিহিতি বলে।
যথা – আজি > আইজ। এই উদাহরণে ‘আজি’ শব্দে ‘ই’ যুক্ত ছিল ‘জ্’ ব্যঞ্জনের সঙ্গে। কিন্তু ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে তা ঐ ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে এবং শব্দটি হয়েছে ‘আইজ’। এরকম – করিয়া > কইর্যা, কালি > কাইল, ভাবিয়া > ভাইব্যা ইত্যাদি।
অভিশ্রুতি
এটি এক প্রকারের ধ্বনির রূপান্তর। অপিনিহিতি জাত ‘ই’ বা ‘উ’ পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে পরবর্তী স্বরের সঙ্গতি ঘটালে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই রীতিকে অভিশ্রুতি বলে।
উদাঃ – রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে, চলিয়া > চইল্যা > চলে, ভাবিয়া > ভাইব্যা > ভেবে ইত্যাদি।
সমীভবন
শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি একে অপরের প্রভাবে কিংবা পারস্পরিক প্রভাবে সমব্যঞ্জনে পরিণত হওয়ার রীতিটিকে সমীভবন বলে। ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতি ব্যঞ্জনসঙ্গতি ও সমীকরণ নামেও পরিচিত।
যেমন – পদ্ম > পদ্দ। এই উদাহরণে মূল শব্দ ‘পদ্ম’ -এর সন্নিকৃষ্ট দুটি ব্যঞ্জনের প্রথম ‘দ্’ -এর প্রভাবে পরবর্তী ‘ম্’ ‘দ্’ তে পরিণত হয়েছে এবং দুটি বিষম ব্যঞ্জন (দ্, ম্) সমব্যঞ্জন (দ্ দ্) হয়েছে। সমীভবন তিন প্রকারের হয় – প্রগত সমীভবন, পরাগত সমীভবন ও অনন্যো সমীভবন।
পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমতাপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন – পক্ব > পক্ক, গলদা > গল্লা, চন্দন > চন্নন ইত্যাদি।
পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে সমতাপ্রাপ্ত হয় তখন তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন – করতাল > কত্তাল, যতদূর > যদ্দুর, কর্ম > কম্ম ইত্যাদি।
যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি পারস্পরিক প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে সমতা অর্জন করে তখন তাকে অনন্যো সমীভবন বলে। যেমন – বৎসর > বচ্ছর, মহোৎসব > মোচ্ছব, উদ্শ্বাস > উচ্ছ্বাস ইত্যাদি।
সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন। উচ্চারণের প্রভাবে শব্দস্থিত দুটি সমব্যঞ্জন বিষম ব্যঞ্জনে পরিণত হলে তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন – শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।
নাসিক্যীভবন
আমাদের উচ্চারণের প্রভাবে শব্দস্থিত কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন যদি লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে তোলে তাহলে ধ্বনি পরিবর্তনের সেই রীতিকে নাসিক্যীভবন বলা হয়।
উদাহরণ – ভাণ্ড > ভাঁড়, চন্দ্র > চাঁদ, ফান্দ > ফাঁদ ইত্যাদি।
অনেক সময় নাসিক্যীভবনের নিয়ম না মেনেই শব্দস্থিত স্বরধ্বনি স্বতোপ্রণোদিত ভাবে আনুনাসিক হয়ে যায়, একেই স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমন – পেচক > পেঁচা, খোকা > খোঁকা ইত্যাদি।
বর্ণদ্বিত্ব
অর্থ গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অনেক সময় শব্দস্থিত কোনো বর্ণের দ্বিত্ব (দু’বার) উচ্চারণ করা হয়। একেই বর্ণদ্বিত্ব বলে। যেমন – একেবারে > এক্কেবারে, সকলে > সক্কলে, সবাই > সব্বাই ইত্যাদি।
সর্বশেষ আপডেট – ২০.০৯.২০২৫